বাংলা ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পদ। আজকের আর্টিকেলে আমরা পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কি কি? ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করব।
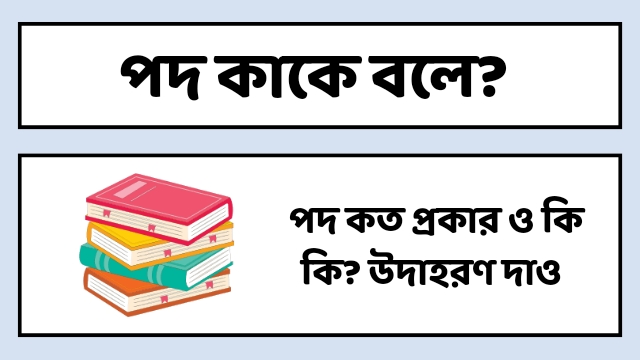
Table of contents
পদ কাকে বলে? পদ কি? উদাহরণ দাও
বাংলা ব্যাকরণে, পদ বলতে বোঝায় বাক্যে ব্যবহৃত অর্থবোধক শব্দ। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, যেকোনো শব্দ যা বাক্যে ব্যবহৃত হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে তাকে পদ বলে। সুতরাং বলা যায়, বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুই পদ এবং বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ। যেমন –
- রহিম একটি বই পড়ছে। (এই বাক্যে, “রহিম” একটি বিশেষ্য পদ (ব্যক্তির নাম), “একটি” একটি বিশেষণ পদ, “বই” একটি বিশেষ্য পদ (জিনিসের নাম), এবং “পড়ছে” একটি ক্রিয়া পদ।)
- মামুন স্কুলে যাচ্ছে। (এই বাক্যে, “মামুন” একটি বিশেষ্য পদ (ব্যক্তির নাম), “স্কুলে” একটি বিশেষণ পদ, এবং “যাচ্ছে” একটি ক্রিয়া পদ।)
- এটি একটি সুন্দর দিন। (এই বাক্যে, “এটি” একটি সর্বনাম পদ, “একটি” একটি বিশেষণ পদ, “সুন্দর” একটি বিশেষণ পদ, এবং “দিন” একটি বিশেষ্য পদ (জিনিসের নাম)।)
পদ কত প্রকার ও কি কি? পদের প্রকারভেদ
পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা –
- সব্যয় পদ
- অব্যয় পদ
সব্যয় পদকে আবার ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো –
- বিশেষ্য
- বিশেষণ
- সর্বনাম
- ক্রিয়া
নবম-দশম শ্রেণীর ব্যাকরণের নতুন সিলেবাসে পদকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা –
- বিশেষ্য
- বিশেষণ
- সর্বনাম
- ক্রিয়া
- ক্রিয়া বিশেষণ
- অনুসর্গ
- যোজক ও
- আবেগ
বিশেষ্য পদ কাকে বলে? বিশেষ্য পদের প্রকারভেদ
বাংলা ব্যাকরণে, যেসব শব্দ ব্যবহার করে ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, বা গুণের নাম বোঝানো হয়, তাদের বিশেষ্য পদ বলে। উদাহরণ –
- ব্যক্তি: রহিম, করিম, শিক্ষক, ডাক্তার
- জাতি: বাঙালি, ইংরেজ, চীনা, জাপানি
- সমষ্টি: পরিবার, দল, দেশ, জাতি
- বস্তু: বই, কলম, টেবিল, ঘর
- স্থান: ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, পৃথিবী
- কাল: বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, শতাব্দী
- ভাব: সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, সাহস
- কর্ম: লেখা, পড়া, গান গাওয়া, খেলাধুলা
- গুণ: সুন্দর, বুদ্ধিমান, লম্বা, মিষ্টি
বিশেষ্য পদের বৈশিষ্ট্য:
- বিশেষ্য পদের সাথে বিশেষণ ব্যবহার করা যায়।
- বিশেষ্য পদের লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি থাকে।
- বিশেষ্য পদ বাক্যের কর্তা, কর্ম, করণ, সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
বিশেষ্য পদকে আবার ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো –
- সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য
- জাতিবাচক বিশেষ্য
- বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য
- সমষ্টিবাচক বিশেষ্য
- ভাববাচক বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য
- গুণবাচক বিশেষ্য
সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য
যে পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, ভৌগলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয়, তাকে সংজ্ঞা বাচক বিশেষ্য বলে। যেমন – আসিফ, দিল্লি, ভারত, মেঘনা, আরব সাগর, বাংলাদেশ, বিশ্বনবী, অগ্নিবীণা ইত্যাদি।
- ব্যক্তিনাম: সীমা, কেয়া, আসিফ, শাওন, মামুন।
- স্থাননাম: শেরপুর, বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ, হিমালয়, লন্ডন, পদ্মা।
- কালনাম: সোমবার, বৈশাখ, জানুয়ারি, রমজান, শুক্রবার, ডিসেম্বর।
- সৃষ্টিনাম: গীতাঞ্জলি, সঞ্চিতা, ইত্তেফাক, অপরাজয় বাংলা।
জাতিবাচক বিশেষ্য
যে পদ দ্বারা কোন এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- মানুষ, গরু, ছাগল, পাখি, ফুল, ফল, গাছ, নদী, সাগর, পর্বত, ইংরেজ, বাংলাদেশী ইত্যাদি।
বস্তবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য
যে পদ দ্বারা কোনো উপাদান বাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন – বই, খাতা, কলম, টেবিল, থালা, বাটি, চাল, ইট, লবণ, চিনি, পানি, আকাশ ইত্যাদি।
সমষ্টিবাচক বিশেষ্য
যে পদ দ্বারা বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- সভা, জনতা, সমিতি, পরিবার, পঞ্চায়েত, ঝাঁক, বহর, দল, বাহিনী, মিছিল, মাহফিল ইত্যাদি।
ভাববাচক বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য
যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন – গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন ( খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), পটন, দেখাশোনা, করা, করানো, পাঠানো, নেওয়া ইত্যাদি।
গুণবাচক বিশেষ্য
যে বিশেষ্য দ্বারা কোন বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন – মধুরতা (মধুর মিষ্টত্বের গুণ), তারল্য ( তরল দ্রব্যের গুণ), তিক্ততা (তিক্ত দ্রব্যের গুণ), তারুণ্য (তরুণের গুণ), সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ, সরলতা, দয়া, আনন্দ, গুরুত্ব, দীনতা, ধৈর্য্য ইত্যাদি।
বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কি কি?
বিশেষণ পদ হল সেইসব শব্দ যা বিশেষ্য, সর্বনাম, বা ক্রিয়ার গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, সময়, স্থান, ইত্যাদি প্রকাশ করে। উদাহরণ –
- গুণ: সুন্দর, বুদ্ধিমান, বড়, লাল
- অবস্থা: ভালো, খারাপ, দুঃখিত, রাগান্বিত
- সংখ্যা: দুটি, তিনটি, অনেক, কম
- পরিমাণ: সামান্য, অধিক, পর্যাপ্ত, অপ্রয়োজনীয়
- সময়: আজ, কাল, সকাল, বিকেল
- স্থান: এখানে, ওখানে, উপরে, নীচে
বিশেষণ পদের বৈশিষ্ট্য:
- বিশেষণ পদ বিশেষ্য, সর্বনাম, বা ক্রিয়ার সাথে ব্যবহার করা হয়।
- বিশেষণ পদের লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি থাকে।
- বিশেষণ পদ বাক্যের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
বিশেষণ পদ দুই প্রকার। যথা –
- নামবাচক বিশেষণ
- ভাববাচক বিশেষণ
নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। নাম বিশেষণ আবার বিভিন্নভাবে বিভক্ত। এগুলো হলো –
- রূপবাচক
- গুণবাচক
- অবস্থাবাচক
- সংখ্যাবাচক
- ক্রমবাচক
- পরিমাণবাচক
- অংশবাচক
- উপাদানবাচক
- প্রশ্নবাচক
- নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক ইত্যাদি।
ভাব বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাই ভাব বিশেষণ। ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার। এগুলো হলো –
- ক্রিয়া বিশেষণ
- বিশেষণীয় বিশেষণ
- অব্যয়ের বিশেষণ
- বাক্যের বিশেষণ
সর্বনাম পদ কাকে বলে? সর্বনাম পদের প্রকারভেদ
সর্বনাম পদ হলো সেইসব শব্দ যা বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। ভাষায় সর্বনাম ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো বিশেষ্যের পুনরাবৃত্তি দূর করা। বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, সর্বনামও অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ্য শব্দের মতো সর্বনাম শব্দের সঙ্গেও বিভক্তি, নির্দেশক, বচন প্রকৃতি যুক্ত হয়। সর্বনাম পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও সাবলীল করা যায়।
উদাহরণ:
- সে বইটা পড়ছে। (এখানে “সে” সর্বনাম)
- তুমি কি খেয়েছো? (এখানে “তুমি” সর্বনাম পদ)
- এটা আমার বই। (এখানে “এটা” সর্বনাম পদ)
সর্বনাম পদের বৈশিষ্ট্য:
- সর্বনাম পদের লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি থাকে।
- সর্বনাম পদ বাক্যের কর্তা, কর্ম, করণ, সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- সর্বনাম পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও সাবলীল করা যায়।
সর্বনাম পদ নয় প্রকার হয়ে থাকে। এগুলো হলো –
- ব্যক্তিবাচক সর্বনাম: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, এ, এরা ইত্যাদি।
- আত্মবাচক সর্বনাম: নিজে, স্বয়ং, খোদ ইত্যাদি।
- নির্দেশক সর্বনাম: এ, এই, এরা, ইনি, উনি, ও, ওই, ওরা ইত্যাদি।
- অনির্দিষ্ট সর্বনাম: কেউ, কোথাও, কিছু, একজন ইত্যাদি।
- প্রশ্নবাচক সর্বনাম: কে, কারা, কাকে, কিসে, কী, কি, কাহার ইত্যাদি।
- সাপেক্ষ সর্বনাম: যারা-তারা, যে-সে, যেমন-তেমন ইত্যাদি।
- পারস্পরিক সর্বনাম: পরস্পর, নিজেরা-নিজেরা ইত্যাদি।
- সকলবাচক সর্বনাম: সবাই, সকলে, সবার, সমস্ত, সকলকে ইত্যাদি।
- অন্যবাচক সর্বনাম: অপর, পর, অমুক, অন্য ইত্যাদি।
অব্যয় পদ কাকে বলে? অব্যয় পদ কত প্রকার ও কি কি?
ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় পদ হল সেইসব শব্দ যা বাক্যের অন্য কোনো পদের সাথে ব্যাকরণগতভাবে যুক্ত থাকে না। অব্যয় পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্যে অতিরিক্ত তথ্য, অর্থ, বা ভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন – এবং, ও, কিন্তু ইত্যাদি।
অব্যয় পদের বৈশিষ্ট্য:
- অব্যয় পদের লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি থাকে না।
- অব্যয় শব্দের একবচন বা বহুবচন হয় না।
- অব্যয় পদ বাক্যের কর্তা, কর্ম, করণ, সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয় না।
- অব্যয় পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্যে অতিরিক্ত তথ্য, অর্থ, বা ভাব প্রকাশ করা হয়।
অব্যয় প্রধানত ৪ প্রকার। যথা –
- সমুচ্চয়ী অব্যয়
- অনন্বয়ী অব্যয়
- অনুসর্গ অব্যয়
- অনুকার বা ধ্বন্যাত্বক অব্যয়
সমুচ্চয়ী অব্যয়: যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে। এটি আবার তিন প্রকার। যথা –
- সংযোজক অব্যয় (ও, এবং, তাই)
- বিয়োজক অব্যয় (কিংবা, বা, নতুবা)
- সংকোচক অব্যয় (অথচ)
অনন্বয়ী অব্যয়: যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিদ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয় তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন – আ মরি বাংলা ভাষা। পাছে লোকে কিছু বলে।
অনুসর্গ অব্যয়: যে সকল অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারক বাচকতা প্রকাশ করে তাদের অনুসর্গ অব্যয় বা পদান্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন- দ্বারা, দিয়া,হইতে, থেকে ইত্যাদি অনুসর্গ অব্যয়।
অনুকার বা ধ্বন্যাত্বক অব্যয়: যে সকল অব্যয় রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয় তাকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্বক অব্যয় বলে। এ জাতীয় ধনাত্মক শব্দের দুবার প্রয়োজন নাম ধনাত্মক দ্বিরুক্তি। ধনাত্মক বিরক্ত দ্বারা বহুত্ব বা আধিক্য ইত্যাদি বুঝায়। যেমন – কড় কড়, গর গর, টুং টাং, কা কা, কল কল ইত্যাদি।
ক্রিয়া পদ কাকে বলে? ক্রিয়াপদের শ্রেণীবিন্যাস
বাক্যে যে পদ দ্বারা কোন কিছু করা, ঘটা, হওয়ায, যাওয়া অর্থাৎ কোন কার্য সম্পাদন বোঝায় থাকে ক্রিয়া পদ বলে। অর্থাৎ যে পদের দ্বারা কোন কার্যসম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন – খাই, পড়ছে, উড়ছে, দেবে ইত্যাদি।
ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা –
- সমাপিকা ক্রিয়া
- অসমাপিকা ক্রিয়া
সমাপিকা ক্রিয়া: সমাপিকা ক্রিয়া হল সেইসব ক্রিয়াপদ যা বাক্যের অর্থ বা ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। সমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বা সমাপ্ত হয়। উদাহরণ –
- কাল ছাত্ররা আসবে। (এই বাক্যে “আসবে” ক্রিয়াপদটি সমাপিকা ক্রিয়া। কারণ এই ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে।)
- আমি গান গাই। (এই বাক্যে “গাই” ক্রিয়াপদটি সমাপিকা ক্রিয়া। কারণ এই ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে।)
- সে কাজ করছে। (এই বাক্যে “করছে” ক্রিয়াপদটি সমাপিকা ক্রিয়া। কারণ এই ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে।)
সমাপিকা ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য:
- সমাপিকা ক্রিয়াপদের কাল, পুরুষ, বচন, বিভক্তি থাকে।
- সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের কর্তার সাথে মানিয়ে চলে।
- সমাপিকা ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না।
অসমাপিকা ক্রিয়া: অসমাপিকা ক্রিয়া হল সেইসব ক্রিয়াপদ যা বাক্যের অর্থ বা ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে না। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বা সমাপ্ত হয় না। বরং, এটি আরও অতিরিক্ত তথ্য, অর্থ, বা ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন – প্রভাতের সূর্য উঠলে………., ভালো করে পড়াশোনা করলে……..
অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য:
- অসমাপিকা ক্রিয়াপদের কাল, পুরুষ, বচন, বিভক্তি থাকে।
- অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের কর্তার সাথে মানিয়ে চলে।
- অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না।
- অসমাপিকা ক্রিয়াপদ অন্য ক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে।
কর্ম পদের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়া আবার চার প্রকার। যথা –
- অকর্মক ক্রিয়া
- সকর্মক প্রিয়া
- প্রযোজক ক্রিয়া
- দ্বিকর্মক ক্রিয়া
গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা-
- যৌগিক ক্রিয়া
- মিশ্র ক্রিয়া
তাহলে আজ এখানেই শেষ করছি। আশা করি পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কি কি? ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা দিতে পেরেছি। ব্যাকরণের আরও টপিক সম্পর্কে জানতে চাইলে নিচের লিংকগুলোতে ক্লিক করুন।
